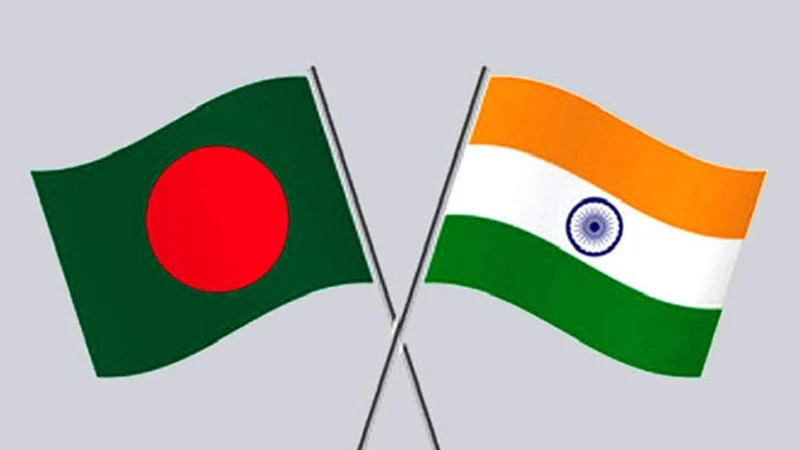পানির জন্য যুদ্ধ: ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের এক সংকটময় দিক
বিশ্বজুড়ে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন, ভবিষ্যতের যুদ্ধ হতে পারে পানিকে ঘিরে। এমনকি, তা পারমাণবিক যুদ্ধেও রূপ নিতে পারে—এমন সতর্কবার্তা দিয়েছেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান ও খ্রিস্টান ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস। ইতোমধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দুই পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ভারত ঘোষণা দিয়েছে, তারা পানিকে কৌশলগত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে প্রস্তুত। সিন্ধু নদ-সম্পর্কিত ঐতিহাসিক চুক্তি স্থগিতের হুমকির প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সাফ জানিয়ে দিয়েছে—পানির প্রবাহ রোধের যেকোনো পদক্ষেপকে যুদ্ধ ঘোষণা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
১৯৬০ সালে বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সিন্ধু পানি চুক্তিতে দুই দেশকে নির্দিষ্ট নদীগুলোর পানি ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হয়। ভারতকে ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রু—এই তিন নদীর নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়, আর পাকিস্তান পায় সিন্ধু, ঝিলাম ও চেনাব নদীর অধিকাংশ পানির অধিকার। এই চুক্তির মূল ভিত্তি ছিল একতরফাভাবে বাতিল বা স্থগিত না করা। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের হুমকি ও রাজনৈতিক বার্তা চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে।
সিন্ধু চুক্তি বহাল থাকা সত্ত্বেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পানিকে ‘অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহারের বক্তব্য কেবল পাকিস্তানের জন্যই নয়, বাংলাদেশের জন্যও বড় উদ্বেগের বিষয়। কারণ, ভারত দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশকে কার্যত পানির দিক থেকে চাপে রেখেছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদী রয়েছে, যার অনেকগুলোর ওপর ভারত upstream-এ বাঁধ ও ব্যারাজ নির্মাণ করেছে। এর ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ কমে গিয়ে বাংলাদেশের কৃষি ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ে, আবার বর্ষায় হঠাৎ করে অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দিয়ে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়।
গত ৫০ বছরের বেশি সময়ে বাংলাদেশের ১৫৮টি নদী শুকিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে বড় কারণ হচ্ছে ভারতের পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ। এই প্রবাহ বাধাগ্রস্ত না হলে নদীগুলো হয়তো শুকিয়ে যেত না। ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যেভাবে পানি-নীতিকে চাপ প্রয়োগের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে, তা একধরনের ‘নরম আগ্রাসন’ বা ‘জলযুদ্ধ’।
ফারাক্কা বাঁধ হচ্ছে বাংলাদেশের ওপর ভারতের পানি নীতির প্রতীক। পঞ্চাশের দশকে ভারত এই বাঁধ নির্মাণ শুরু করলেও, সেটি চালু হয় ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে। পরীক্ষামূলক ১০ দিনের জন্য চালু করা ফারাক্কা বাঁধ আজও চালু রয়েছে। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার সরকারের সময় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও, বাস্তবে সেটি কার্যকর হয়নি। চুক্তিতে উল্লেখিত পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা তো দূরের কথা, ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসেই বাংলাদেশ পেয়েছিল মাত্র ৬,৪৫৭ কিউসেক পানি—যা ছিল রেকর্ড সর্বনিম্ন।
চুক্তির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে, এতে আন্তর্জাতিক সালিসি বা আরবিট্রেশনের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে ভারত যদি চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে, তবে বাংলাদেশের জন্য কোনো আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থায় যাওয়ার সুযোগ নেই। একই সময়ে ভারতের সঙ্গে নেপালের মহাকালী চুক্তি ও পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু চুক্তিতে কিন্তু আন্তর্জাতিক সালিসি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
এছাড়া ভারতের তিস্তা নিয়ে কোনো চুক্তিই আজ পর্যন্ত হয়নি। ২০১১ সালে মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরে চুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হলেও, ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কারণে তা আলোর মুখ দেখেনি। অথচ তিস্তার পানি বাংলাদেশে কৃষিকাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সরকার মুখে কড়া অবস্থান নিলেও, পরে ভারতের স্বার্থে ট্রানজিট সুবিধা, বিদ্যুৎ কেনা এবং বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে—যা অনেকের মতে দেশের স্বার্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে চীনের আগ্রহের কারণে। চীন তিস্তা প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চাইলেও ভারতের বিরোধিতায় তা আটকে গেছে। তবে সম্প্রতি ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে চীন সফরের সময় বাংলাদেশ ৫০ বছরের একটি নদী-ব্যবস্থাপনা মাস্টারপ্ল্যান চেয়েছে। এতে নদী অববাহিকা-ভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
বর্তমান বাস্তবতায়, বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে পানির কূটনীতিতে ভারসাম্যপূর্ণ ও কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ। ভারত যদি রাজনৈতিক ও কৌশলগত কারণে নদীগুলোর পানি প্রত্যাহার অব্যাহত রাখে, তাহলে বাংলাদেশের উচিত চীনের সঙ্গে যৌথভাবে পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ বাড়ানো। ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে বর্ষার অতিরিক্ত পানি সংরক্ষণ এবং শুষ্ক মৌসুমে তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।
একটি বিষয় স্মরণে রাখা প্রয়োজন—ভারত যখন ফারাক্কা বাঁধ চালু করেছিল, তখন তার প্রধান লক্ষ্য পাকিস্তান ছিল না, ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। পানিকে রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করে প্রতিবেশীদের ওপর চাপ প্রয়োগের এই নীতি একুশ শতকে নতুন করে মূল্যায়ন করার সময় এসেছে।
সূত্রঃ আমার দেশ